বাংলাদেশে গমের ব্লাস্ট রোগ: জীবাণুর বৈশিষ্ট্য এবং দমন ব্যবস্থাপনা উদ্ভাবনে গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা
ড: মুহম্মদ আশিক ইকবাল খান [১] এবং ড: মো: শাহজাহান কবির [২]
গম বাংলাদেশের একটি সম্ভাবনাময়ী ফসল। এটি চাষাবাদে পানির চাহিদা কম হওয়াতে এবং ধানের আবাদ অলাভজনক হয়ে পড়ায় গমের আবাদে কৃষকরা দিন দিন আগ্রহী হচ্ছেন। আর ঠিক সেই সময়, সর্বনাশা ব্লাস্ট রোগের আক্রমন, গম চাষে একটি বড় ধরনের হুমকি হয়ে দাড়িয়েছে। ১৯৮৫ সালে ব্রাজিলে প্রথম এ রোগটি দেখা দিলেও এশিয়া মহাদেশের মধ্যে বাংলাদেশেই প্রথম এবার রোগটি দেখা দেয়। যেহেতু রোগটি এ দেশে নতুন তাই বিজ্ঞানী, সম্প্রসারনকর্মী, কৃষক এমনকি নীতি নির্ধারকদের মধ্যেও রোগটি নিয়ে বিশেষ আগ্রহ দেখা দিয়েছে।
রোগটি দেখতে কেমন? গাছের কোথায় হয়? ক্ষতির পরিমান কেমন? এ সমস্ত বিষয়ে ইতমধ্যে কমবেশী সবাই জেনে গেছেন। তাই এই সম্পর্ক্যে কিছু লিখবো না। তবে একটা কথা বলে রাখি, যেহেতু রোগটির জীবাণু বীজের মধ্যেও থাকতে পারে, তাই গম বোনার সময় সুন্দর করে বীজ শোধন করে লাগিয়ে নিশ্চিন্তে বসে থাকলে কিন্তু বিপদে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা আছে। এ রোগটি প্রধানত বাতাসের মাধ্যমে ছড়ায় এবং বীজ শোধন করে লাগালেও পরবর্তীতে একই এলাকার অন্যের জমিতে এ রোগটি দেখা দিলে, তখন সেখান থেকে আপনার জমিতেও বাতাসের মাধ্যমে রোগটি আসতে পারে। গমের জাত, বৃদ্ধির পর্যায়, জীবাণুর রোগ করার ক্ষমতা এবং আবহাওয়ার উপাদান দ্বারা রোগটির আক্রমনের তীব্রতা প্রভাবিত হয়।
গমের ব্লাস্ট রোগ যে জীবাণু দিয়ে হয়ে থাকে ঠিক একই প্রজাতীর জীবাণু দিয়ে ধানেরও ব্লাস্ট রোগ হয়, তবে দ’ুটোর রেস দু’রকম। যেহেতু একই প্রজাতীর জীবাণু দিয়ে ধান ও গমে একই রোগ ছড়ায়, আর তা-ই আজ আমাদের মাঝে রোগটির উৎস নিয়ে নানা বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। আমরা চেষ্টা করবো সেই বিতর্কিত বিষয় গুলো নিয়েই শুধু আলোচনা করতে। আজ থেকে ৩১ বছর আগে ব্রাজিলের পারানা রাজ্যে যখন প্রথম রোগটি দেখা দেয় তখনও একই ভাবে বিতর্কের সৃস্টি হয়ে ছিল এবং তা সমাধানের জন্য ব্যাপক গবেষণাও হয়েছে। তাদের গবেষণা লব্ধ তথ্যের আলোকেই মূলত আলোচনা করব। প্রথমেই শুরু করি ব্লাস্ট রোগের জীবাণুর নামকরন দিয়ে। কেউ কেউ এ রোগের জীবাণুর নাম Magnaporthe oryzae, আবার কেউ কেউ Pyricularia oryzae বলছেন। একজন বিশিষ্ট্য বিজ্ঞানী তো মন্তব্যই করে বসেছেন যে, একই রোগের জীবাণুর দুই রকম নাম হয় কিভাবে? আসলে ব্লাস্ট রোগের জীবাণুর নাম দু’টিই। এরা যখন যৌন পদ্ধতিতে জীবন চক্র সম্পন্ন করে তখন তাদের নাম হয় Magnaporthe oryzae, আর যখন একই জীবাণু অযৌন পদ্ধতিতে জীবন চক্র সম্পন্ন করে তখন বলে Pyricularia oryzae। তবে প্রকৃতিতে যৌন পর্যায়টা পাওয়া খুবই বিরল এবং গম গাছে প্রধানত অযৌন স্পোর কনিডিয়া দিয়েই আক্রমন করে। বিভিন্ন জার্নাল ঘাটলে দেখা যায়, অধিকাংশ বিজ্ঞানীরাই জীবন চক্রের পর্যায় উল্লেখ করে দু’টো নামই ব্যবহার করেন।
একটা প্রশ্ন সবার মনে এখন খুব বেশী ঘুরপাক খাচ্ছে, আর সেটি হলো এ রোগের জীবাণু আমাদের দেশে আসলো কোথা থেকে? আবার অনেকেই ভাবছেন, ধানের ব্লাস্ট রোগের জীবাণুতো ধান থেকে গমে জাম্প করলো না? এ রকম আরো কত কি? এই প্রবন্ধটি লেখার আগে আমরা আমেরিকার কানসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. ক্রুজ এবং জাপানের ড. হায়াসি এর সাথে এ বিবষয় গুলো নিয়ে দীর্ঘ সময় আলোচনা করি। তারা দু’জনই দীর্ঘদিন ধনের গমের ব্লাস্ট রোগ নিয়ে কাজ করছেন। তাদের মতে ব্লাস্ট রোগের জীবাণু রোগ করার ব্যাপারে খুবই নির্দিষ্ট। ধানের ব্লাস্ট রোগের জীবাণু ধানের একটি জাতে রোগ করলে অন্য জাতে রোগ নাও করতে পারে। আবার ধানের জীবাণু গমে বা গমের জীবাণু ধানে মহামারি আকারে রোগ করতে পারে না। এ রোগের জীবাণু অনুবিক্ষণ যন্ত্রে দেখলে সব এক রকমই দেখায়, এমনকি এদের ITS সিকোয়েন্স তথ্যের মধ্যেও মিল পাওয়া যায় (রেফারেন্স-৪)। কিন্তু এক একটি জীবাণুর রোগ করার ক্ষমতা এক এক রকম। যাকে রোগতত্ত্বের ভাষায় ফিজিওলোজিকাল রেস বা প্যাথোটাইপ বলে। ব্লাস্ট রোগের জীবাণুর রেসের সংখ্যা অন্য রোগের জীবাণু অপেক্ষা একটু বেশী। ব্রি-র এক গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে ধানের ব্লাস্ট রোগের ৩৩১টি জীবাণুর মধ্যে ২৬৭টি রেস আছে (রেফারেন্স-১)। বিভিন্ন গবেষণার তথ্যের উপর ভিত্তি করে আমরা পরিস্কার ভাবে বলতে চাই, ধানের ব্লাস্ট রোগের জীবাণু বাঁচার তাগিদে হয়ত গমের উপর থাকতে পারে কিন্তু কখনই গমে মহামারি আকারে রোগ সৃষ্টি করতে পারে না। আবার ঠিক গমের বা ঘাসের ব্লাস্ট রোগের জীবাণু ধানে রোগ তৈরী করতে পারে না (রোফারেন্স-২, ৩, ৪)। তারপরও যদি কেউ নিশ্চিত ভাবে দেখতে চান তবে যেটা করতে হবে- প্রথমে গমের ১০টি জাত তার মধ্যে অবশ্যই ২টি এ রোগের প্রতি সংবেদনশীল হতে হবে এবং ধানের ১০টি জাত একই ভাবে সংবেদনশীল জাত LTH ও US2 সহ পরীক্ষা করতে হবে। এর পর গমের ব্লাস্ট রোগে মহামারী আকার ধারন করেছে এমন জমি থেকে কমপক্ষে ৫টি জীবাণু এবং ধান থেকে সংগৃহিত ৫টি জীবাণু নিয়ে আলাদা আলাদা ভাবে ইনোকুলেশন করে দেখতে হবে যে, ধানের জীবাণু গমে বা গমেরটা ধানে রোগ করতে পারে কিনা এবং তা মহামারী আকার ধারন করতে পারে কিনা। ধানের জীবাণু যদি ধানে রোগ করে কিন্তু গমে না করে বা গমের জীবাণু যদি গমে রোগ করে কিন্তু ধানে না করে, তখন আমাদের কাছে বিষয়টি পরিস্কার হয়ে যাবে। তবে এ ক্ষেত্রে অবশ্যই পাতা ব্লাস্ট এবং হেড ব্লাস্ট দু’টোই চেক করতে হবে। ড. ক্রুজের মতে গমের ব্লাস্ট রোগের জীবাণু ধানে বা ধানেরটা গমে সাধারনত রোগ করতে পারে না। তারপরও পারিপার্শ্বিকতার কারনে যদি রোগ তৈরী করেও তবে তা কখনোই ব্যাপকতা লাভ করতে পারে না বা মহামারী আকার ধারন করে না (রেফারেন্স-৪)। কারন স্ব স্ব ফসলের জীবাণু নিজস্ব পোষকে যেভাবে রোগের লক্ষণ প্রকাশ করে অন্য ফসলে তা করতে পারে না। আমাদের এক বিজ্ঞ বন্ধু তার সাক্ষাতকারে উল্লেখ করেছেন যে, গমের ব্লাস্ট রোগের জীবাণু ধান থেকে গমে জাম্প করেছে এবং রেফারেন্স হিসেবে ড. ইগারাশি এর নাম উল্লেখ করেছেন। জানিনা পর্তুগীজ ভাষায় লেখা প্রবন্ধটি উনি ঠিকতম পড়তে পেরেছেন কি-না। বিজ্ঞানী ইগারাশি উনার পেপারে উল্লেখ করেছেন গমের জীবাণুর পোষক হচ্ছে বার্লি, ওট, রাই এবং ভূট্টা, লক্ষ্য করতে হবে উনি ধানের নাম উল্লেখ্য করেননি (রেফারেন্স-৩)। উনি যেটা উল্লেখ করেছেন, সেটা হলো, ধানের ব্লাস্ট রোগের জীবাণু গমের উপর যেতে পারে। কিন্তু এ কথা বলেননি যে, ব্রাজিলে ১৯৮৫ সালে ধানের জীবাণু গমে গিয়ে মহামারী আকার ধারন করেছে বা গমের মহামারী ধানের ব্লাস্ট রোগ জাম্প করে গমে গিয়ে হয়েছে। এরপর অনেক দিন পার হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত বিষয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। মজার বিষয় হলো বিজ্ঞানী ইগারাশি ১৯৯৩ সালে বিজ্ঞানী উরাসিমা এর সাথে Plant Disease নামক জার্নালে একটা প্রবন্ধ প্রকাশ করেন (রেফারেন্স-৩)। সেখানে স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন যে, ধানের ব্লাস্ট রোগের জীবাণু গমে রোগ করতেও পারে আবার নাও পারে কিন্তু গমের জীবাণু ধানে রোগ করতে পারে না। দু’টো জীবাণুর জেনেটিক বৈশিষ্ট্যই আলাদা। অনেকে হয়ত বলতে পারেন, ধানের জীবাণু গমে গিয়ে গমের জীবাণুর সাথে মিউটেশন হয়ে গমে মহামারী আকার ধারন করেছে। তার উত্তরও বিজ্ঞানীরা দিয়েছেন। আর সেটা হলো ধানের জীবাণুর সাথে গমের জীবাণুর যৌন মিলনও অসম্পূর্ণ অর্থাৎ এদের পরস্পরের মধ্যে ক্রসিং করলে এরা পেরিথেসিয়া তৈরী করতে পারে না (রেফারেন্স-৩)। এরপরও একটা সন্দেহ থেকে যাচ্ছে যে, যেহেতু ধানের জীবাণু গমের উপর আশ্রয় নিতে পারে, তাহলে তো গমের জীবাণু ধান থেকে কেন আসতে পারেবে না? হ্যাঁ, আমাদেরও সেটাই প্রশ্ন ছিলো জাপানী বিজ্ঞানী ড. হায়াসির কাছে। উনি স্পস্ট করে একই কথা বলেছেন যে, গমের জীবাণু ধানে যেতে পারে কিন্ত সেক্ষেত্রে কখনোই ধানের জীবাণু দিয়ে গমে মহামারী হবে না। গমের মহামারি হতে হলে গমের জীবাণুই লাগবে। দু’টো জীবাণুর রোগ করার ক্ষমতা কখনোই এক না। বিজ্ঞানী ফারম্যানও তার প্রকাশিত প্রবন্ধে একই কথা উল্লেখ করেছেন (রেফারেন্স-৪)। এমনকি সম্প্রতিকালে নেচারে প্রকাশিত প্রবন্ধও জিন সিকোয়েন্স এর উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানীরা একই কথা বলেছেন যে, বাংলাদেশের গমে ব্লাস্ট রোগের জীবাণুর সাথে ব্রাজিলের গমের জীবাণুর মিল আছে। তারা একবারও বলেননি যে, বাংলাদেশের গমের ব্লাস্ট রোগের জীবাণুর সাথে বাংলাদেশের ধানের ব্লাস্ট রোগের জীবাণুর সাথে মিল আছে (রেফারেন্স-৬)। অতএব আমার বন্ধুরা, এখন পরিস্কার হয়েছে যে, ধানের এবং গমের ব্লাস্ট রোগের জীবাণু এক নয়, একে অন্যের উপর কখনোই মহামারী আকার ধারন করতে পারে না এবং বাংলাদেশে গমের ব্লাস্ট রোগের জীবাণু ধান থেকে আসেনি, এটার সাথে ব্রাজিলের জীবাণুর মিল আছে।
এখন প্রশ্ন হচ্ছে রোগটি দমনে আমারা কোথা থেকে আমাদের গবেষণা শুরু করব? এবং কিভাবেই বা শুরু করব? জাপানে ২০০৫ সালে ব্যাপক আকারে ধানে ব্লাস্ট রোগের আক্রমন হয়। আর রোগটি দমনে গবেষণা করার জন্য জাপান এশিয়া মহাদেশের ১০টি দেশ নিয়ে একটি নেটওয়ার্ক তৈরী করে। সৌভাগ্য ক্রমে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) সেই নেটওয়ার্কের একজন সদস্য হিসেবে কাজ করছে। ব্রি-র সেই অভিজ্ঞতার আলোকে এই অধ্যায়টি আলোচনা করব। রোগ দমনে মূলত দুটি উপায়- জীবাণুনাশকের ব্যবহার এবং রোগ প্রতিরোধী জাতের আবাদ। ব্রি ধানের ব্লাস্ট রোগ দমনে ট্রায়সাইক্লাজল গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমন: ট্রুপার অথবা মিক্সড ছত্রাকনাশক যেমন: নেটিভোসহ বেশ কয়েকটি ছত্রাকনাশক স্প্রে করে পাতা ব্লাস্ট এবং শীষ ব্লাস্ট দমনে ভাল ফল পেয়েছে। বিধায় প্রথমে ধানের জন্য উপযোগী ছত্রাকনাশক গুলো নিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে, গমে কাজ করে কি-না। তবে এক্ষেত্রে পাতা ব্লাস্ট এবং হেড ব্লাস্ট দু’টোর ক্ষেত্রেই উপযোগীতা পরীক্ষা করতে হবে। ব্লাস্ট রোগের প্রতি সংবেদনশীল গমের জাতে কৃত্রিম ভাবে ইনোকুলেশন করে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে গবেষণাটি করতে হবে। আশা করি ভাল কোন ছত্রাকনাশক পাওয়া যাবে, যা আমাদের কৃষকদেরকে কিছুটা হলেও উপকার করবে। তবে শুধু ছত্রাকনাশক এর উপর নির্ভর করলে চলবে না। কারন সব রোগই যখন মহামারী আকার ধারন করে তখন আর ছত্রাকনাশকে কাজ করে না। আবার আমাদের কৃষকেরা রোগের ক্ষতি চোখে না দেখা পর্যন্ত ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করতে চায় না। কিন্তু শীষ ব্লাস্ট রোগে একবার শীষ শুকিয়ে গেলে ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করে আর কোন কাজ হয় না। তাই এ রোগটি দমনে সবচেয়ে লাভজনক উপায় হচ্ছে রোগ প্রতিরোধী জাতের আবাদ। কিন্ত রোগ প্রতিরোধী জাতের খুব অভাব এবং নতুন জাত উদ্ভাবন করাও কোন সহজ কাজ নয়। আর এ কাজে পদ্ধতিগত ভুল হলে তা আর কোন কাজে আসবে না। ধানের ব্লাস্ট রোগ প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবনের অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা এখন গমের রোগ প্রতিরোধী জাত উদ্ভভাবনের কাজটি ধাপে ধাপে আলোচনা করছি।
প্রথমে আমাদেরকে বাংলদেশের জন্য একটি ডিফারেনসিয়াল সিসটেম তৈরী করতে হবে, আর তা দিয়েই ব্লাস্ট রোগের জীবাণুকে গ্রুপিং করতে হবে। যেহেতু এ রোগের জীবাণুর রেসের পরিমান একটু বেশী আর সব রেসের বিপরীতে রোগ প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবন করাও সম্ভব নই, তাই মেজর রেস নির্দিষ্ট করে সেটি নিয়ে এগুতে হবে। তার জন্য আমাদেরকে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কমপক্ষে গমের ব্লাস্ট রোগের ১০০টি জীবাণু সংগ্রহ করতে হবে। তারপর গমের কমবেশী ১০০টি জাতে ইনোকুলেশন কওে তাদের রোগ করার ক্ষমতা নির্ণয় নির্দিস্ট স্কেল অনুযায়ী মাপতে হবে। এক্ষেত্রে পাতা ব্লাস্ট এবং শীষ ব্লাস্ট দু’টো লক্ষণেরই তথ্য নিতে হবে। এক একটি জীবাণু এক এক জাতে এক এক মাত্রায় রোগ তৈরী করবে এবং প্রপ্ত উপাত্য দিয়ে দুই ভাবে গ্রুপিং করতে হবে। একবার জাত গুলোর উপর ভিত্তি করে জীবাণুকে, আরেকবার জীবাণুর উপর ভিত্তি করে জাতকে। এখান থেকে আমারা জীবাণুর মেজর গ্রুপ নির্ণয় করতে পারবো এবং প্রতি গ্রুপ থেকে সবচেয়ে স্বাস্থ্যবান জীবাণুটি নির্বাচন করে, তার বিপরীতে আমাদের জাত তৈরী করতে হবে। আবার জাত গুলোর প্রতিটি গ্রুপ থেকে একটি করে জাত নিয়ে কয়েকটি জাত মিলে একটা সেট তৈরী করতে হবে, যা পরবর্তীতে জীবাণুর রেস নির্ণয়ে ব্যবহৃত হবে। বিজ্ঞানের ভাষায় এই নির্বাচিত জীবাণু গুলোর সেটকে ডিফারেনসিয়াল আইসুলেট এবং জাত গুলোকে ডিফারেনসিয়াল ভ্যারাইটি বলে। আর একত্রে এদেরকে ডিফারেনসিয়াল সিস্টেম বলে। এটিই হচ্ছে রোগ প্রতিরোধী জাত তৈরী করার প্রথম ধাপ। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ডিফারেনসিয়াল সিস্টেম তৈরী করে লাভ কি? আর জাত তৈরীতে এটি কোন কাজে লাগবে? প্রথমে বলি, জীবাণুর কথা। আমারা রোগ প্রতিরোধী নতুন যে জাতটি তৈরী করব সেটিকে অবশ্যই বেশীর ভাগ জীবাণুর বিপরীতে প্রতিরোধী হতে হবে। কিন্তু একটা একটা করে প্রতিটি জীবাণুর বিপরীতে পরীক্ষা করা সম্ভব নই, আর সেই কাজটিই আমাদের নির্বাচিত ডিফারেনসিয়াল আইসুলেট করবে। এছাড়াও বর্তমানে আমাদের উচ্চ ফলনশীল গমের জাত গুলোর মধ্যে যে গুলো ডিফারেনসিয়াল আইসুলেটেরে বিপরীতে রোগ প্রতিরোধী হবে, সেগুলোকেও আমরা রোগপ্রবন এলাকাতে চাষাবাদের জন্য এখনি সুপারিশ করতে পারবো। নতুন নতুন জায়গায় রোগ দেখা দিলে, সেটা কি নতুন কোন উৎস থেকে আগত নতুন কোন রেস দিয়ে আক্রমন হলো কি-না, তা নির্ণয়ের জন্য ডিফারেনসিয়াল ভ্যারাইটি ব্যবহার করা হবে। যদি নতুন জায়গায় আক্রান্ত জীবাণু ডিফারেনসিয়াল ভ্যারাইটির সাথে পূর্বের রিয়াকশন থেকে ভিন্ন রিয়াকশন দেয় তবে আমারা বলতে পারবো নতুন কোন রেসের আবির্ভাব হয়েছে। তাছাড়া রোগ প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে প্রথম যেটি দরকার তা হচ্ছে রোগ প্রতিরোধী জিনের উৎস। আমাদের যে জাতটি বেশীর ভাগ রেসের বিপরীতে প্রতিরোধী হবে তাকে আমরা রোগ প্রতিরোধী জিনের উৎস হিসেবেও ব্যবহার করতে পারবো। এই ভাবে ডিফারেনসিয়াল সিসটেম তৈরী করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান একই সিসটেম ব্যবহার করে কাজ শুরু করলে, আমারা আশা করি অল্প সময়ের মধ্যে একটি সুন্দর রেজাল্ট পাওয়া সম্ভব হবে। আর তা না হলে একেক প্রতিষ্ঠান এক এক ভাবে কাজ করে অনেক রোগ প্রতিরোধী জাত তৈরী করবে, কিন্তু কোন টা-ই বাংলাদেশের জন্য উপযোগী বা টেকশই হবে না। উদাহরনস্বরূপ যশোরের বিজ্ঞানীরা যে জাতটিকে রোগ প্রতিরোধী বলে দাবী করবেন মেহেরপুরওয়ালাদের কাছে সেটা রোগ প্রতিরোধী নাও হতে পারে, আর সেটাই স্বাভাবিক। কারন দু’জায়গার বিজ্ঞানীরা দু’রকম রেসের উপর ভিত্তি করে জাত উদ্ভাবন করবেন। আরো মজার ব্যাপার হবে যদি রেস নির্দিষ্ট না করে জাত উদ্ভাবন করা হয়, তাহলে একই জায়গায়, একই ট্রায়েলে কখনো রোগ প্রতিরোধী হবে আবার কখনো সংবেদনশীল হবে। অনেকে হয়ত বলবেন জিন সিকুয়েন্স করেও তো কাজটি করা যায়। অবশ্যই করা যায়, কিন্তু আপনি একা কয়টি রেসের সিকোয়েন্স করবেন? বা দেশে কয়টি জিন সিকোয়েন্স ল্যাব তৈরী করবেন? তার পরের প্রশ্নটি হচ্ছে জিনসিকোয়েন্স এর তথ্য রোগ প্রতিরোধী জাত তৈরীতে কিভাবে প্রয়োগ করবেন? হয়ত ভাবছেন ওয়েবসাইট খুলে রাখলে বিদেশীরা তাদের দেশের জীবাণুর avir জিনের তথ্য দিবে, আর সেটি ব্যবহারর করে বাংলাদেশের জন্য জাত তৈরী হবে। হ্যাঁ, বিদেশীদের avir জিনের তথ্য হয়ত আমরা পাবো কিন্তু মনে রাখতে হবে আমার দেশের জন্য রোগ প্রতিরোধী জাত তৈরী করতে হলে আমার দেশের জীবাণুর avir জিনের তথ্যই প্রয়োজন, যেটা আমাদেরকেই তৈরী করতে হবে। কিন্তু Gene for Gene তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে তৈরী কার ডিফারেসসিয়াল সিসটেম ব্যবহার করে সবার অংশগ্রহনে, অতি অল্প সময়ে, আমারা সারা বাংলাদেশের তথ্য এবং সাথে সাথে রোগ প্রতিরোধী জিনের উৎসও পেতে পারি। আর বিদেশীদের জিন সিকোয়েন্স এর তথ্য ব্যবহার করে, জিন এডিটিং এর মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধী জাত তৈরীতে কত সময় লাগবে? এবং উদ্ভাবিত জাত আমাদের দেশের জন্য কতটুকু উপযোগী এবং টেকসই হবে? তার উত্তরটা আমাদের বায়োটেকনোলজিস্ট বন্ধুদের উপরই ছেড়ে দিলাম। তবে বায়োটেকনোলজিস্টরাও নির্বাচিত ডিফারেনসিয়াল আইসুলেট কি ধরনের avir জিন বহন করছে, তা জিন সিকোয়েনসের মাধ্যমে নির্ণয় করে রোগ প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।
ব্লাস্ট রোগ প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবনের এরপরের কাজটি হচ্ছে বর্তমানে উচ্চ ফলনশীল গমের জাত তৈরীতে যে ব্রিডিং পদ্ধতি অনুসরন করা হয় (Backcross breeding) সেভাবে করলেই হবে। রোগ প্রতিরোধী জিনের উৎসতো আমাদের ডিফারেনসিয়াল ভ্যারাইটির মধ্যে আছেই, আর ডিফারেনসিয়াল আইসুলেটের মেজর গ্রুপ থেকে নির্বাচিত জীবাণুটি ব্যবহার করে, এবং ডিএনএ মার্কারের সাহায্য নিয়ে কাজটি সহজভাবে করা যাবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে যে, প্রতি ধাপেই আমাদের কাঙ্খিত গাছটি নির্বাচনের ক্ষেত্রে ডিফারেনসিয়াল আইসুলেট ব্যবহার করে বাস্তবিক ভাবেই গাছটি রোগ প্রতিরোধী কি-না, তা পরীক্ষা করে নিতে হবে। আমরা আশা করছি এভাবে কাজ করলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সবার অংশ গ্রহনে বাংলাদেশের জন্য উপযোগী ব্লাস্ট রোগ প্রতিরেরাধী গমের জাত উদ্ভাবন করে, গম চাষে বর্তমানের হুমকি দূর করে, বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা সম্ভব হবে।
পরিশেষে একাজটি বেগবান করার জন্য আমাদের প্রস্তাব হচ্ছে : বাংলাদেশ গম গবেষণা ইনস্টিটিউট এর নেত্রিত্তে বিএডিসি কে সাথে নিয়ে একটি টিম গঠন করা যেতে পারে। যার সার্বিক ব্যবস্থাপনায় থাকবেন বিএআরসি। যদি অন্য কোন প্রতিষ্ঠান যেমন: বিশ্ববিদ্যালয় এ কাজে আগ্রহ প্রকাশ করে তবে তাদেরকেও সাথে রাখা যেতে পারে। আর যেহেতু ব্রি-র একাজে অভিজ্ঞতা আছে বিধায় ব্রি টেকনিক্যাল এক্সপার্ট হিসেবে উক্ত টিমের সাথে কাজ করতে পারে।
রেফারেন্সঃ
- Khan MAI., Ali, MA., Monsur MA., Kawasaki-Tanaka A., Hayashi N., Yanagihara S., Obara M., Mia MAT, Latif MA. And Fukuta Y. 2016. Diversity and distribution of rice blast (Pyricularia oryzae Cavara) races in Bangladesh. Plant Disease (Accepted for publication).
- Prabhu AS., Corsi de Filippi MC. and Castro N. 1992. Pathogenic variation among isolates of Pyricularia oryzae affecting rice, wheat, and grasses in Brazil. Tropical Pest Management 38(4):367-371.
- Urashima AS., Igarashi S. and Kato H. 1993. Host range, mating type, and fertility of Pyricularia grisea from wheat in Brazil. Plant Disease 77(12):1211-1216.
- Farman ML. Pyricularia grisea isolates causing gray leaf spot on perennial ryegrass (Lolium perenne) in the United State: relationship to griseaI isolates from other host plants. Phytopathology 92(3):245-254.
- Maciel JLN., Ceresini PC., Castroagudin VL., Zala M., Kema GHJ. And McDonald BA. 2014. Population strudture and pathotype diversity of the wheat blast pathogen Magnaporthe oryzae 25 years after its emergence in Brazil. Phytopathology 104(1): 95-107.
- Callaway E. 2016. Devastating wheat fungus appears in Asia for first time. Nature 532:421-422.
[Featured photo source: https://nifa.usda.gov/blog/wheat-blast-bangladesh-and-biosecurity-nifa-funded-research-works-global-food-security]
[১] উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ এবং [২] পরিচালক (প্রশাসন ও সাধারন পরিচর্যা), বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর। যোগাযোগ: ইমেইল: ashikjp@gmail.com
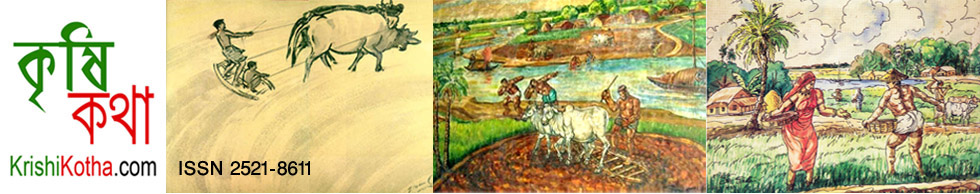
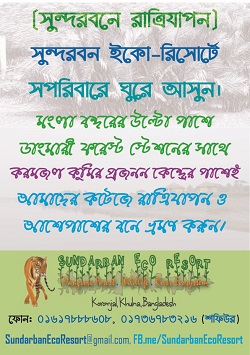




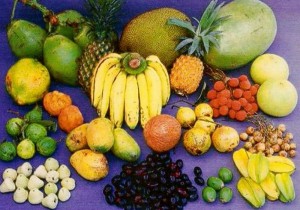






 Visit Today : 92
Visit Today : 92 Total Visit : 173147
Total Visit : 173147