হাওরে ধান উৎপাদন বনাম কৃষক সুরক্ষা — ড. নিয়াজ পাশা
” বৈশাখ মাস” এ হাওর-ভাটি এলাকায় বোরো ধান কাটার ধুম। নতুন ধান মানেই খুশির বিষয়-আশয়। ধান কাটাকে কেন্দ্র করে সর্বত্র বিরাজ করে সরব উচ্ছ্বাস, আনন্দ উৎসব। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে অসংখ্য মানুষ (দা-ওয়াল) আসে ধান কাটতে, সদাই বিক্রি করতে । এখানে সেখানে গজিয়ে উঠে হাজারো রকমের ভাসমান দোকান; সরগরম থাকে রাত দিন ২৪ ঘন্টা, মানুষে-মানুষ গিজগিজ করে সবখানে। চারিদিক থাকে নতুন ধানের মৌ মৌ গন্ধ বিভোর,মেলার আয়োজন। উৎসব আমেজের ভাব থাকার কথা থাকলেও এ বছর কেমন যেন মৃয়মান, কৃষক হতাশ ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। দীর্ঘ খরার পর, এ বছর আগাম বন্যার তেমন উৎপাত নেই, উৎপাদন ভাল হয়েছে, তবু কৃষকের মুখে হাসি নাই। কারণ ধানের উপযুক্ত দাম নাই। সব কিছুই বিনিময় হয় নতুন ধানে। মাঠের আনন্দ উবে গেছে দামের নিম্নমুখী স্রোুতে। পানির দরে, উৎপাদন খরচের চেয়ে অনেক কম দামে তাঁদের ধান বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। এ অবস্থায় সারা বছরের নিত্য প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন চাহিদার উপোষের যোগান দিতে এবং লগ্নি, ঋণ, কর্জ হাসিলের চিন্তায় কৃষক দিশেহারা। কম দামে ধান বিক্রি করে আর সব কিছু অধিক দামে কিনতে গিয়ে কৃষকের নাভিশ্বাস অবস্থা।
খাদ্য নিরাপত্তার কারিগর বা পাহারাদার হচ্ছে কৃষক। হাওরের কৃষকগণ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এমনকি গভীর রাত পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে, অকাল, আগাম বন্যা, খরা ও প্রকৃতির সাথে সংগ্রাম করে আমাদের জন্য ফসল উৎপাদন করে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। হাওরে প্রচলিত ”যার আছে সাত পুত, তের নাতি, সে যেন করে গিরস্থি ” প্রবাদ বাক্য হতেই কৃষির সাথে হাওরবাসি কৃষক পরিবারের সকল সদস্যের ওৎপ্রোতভাবে জড়িত থাকা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের জানান দেয়। হাওরে সারা বছর মাত্র একটি বোরো ধান আবাদ হয়ে থাকে। কার্তিক/অগ্রাহায়ণ হতে বৈশাখ/জৈষ্ঠ্য মাস পর্যন্ত এ ধান চাষ হয়। বাকী সময়টা হাওরের জমি থাকে অথৈ পানির নীচে। বলা হয়ে থাকে, হাওরে বছর হয় ছ’মাসে। দেশে উৎপাদিত মোট ধানের প্রায় এক পঞ্চমাংশ ধান এ হাওরে উৎপাদিত হয়। পানির দ্যাশ, গানের দ্যাশ, ঊড়া পংখির দ্যাশ-হাওর-ভাটি এলাকা ’বাংলার শস্য ভান্ডার’ হিসাবেও পরিচিতি পেয়েছে।
এ ধান উৎপাদন করতে হাওরবাসি কৃষককে পদে পদে ভোগান্তি বা বিড়ম্বনার মুখোমুখি হতে হয়। হাওর এলাকায় এখনো বড় অবস্থাপন্ন কৃষক/অকৃষক পরিবারের হাতে অধিকাংশ জমি থাকায় প্রান্তিক কৃষককে তাঁদের কাছ হতে জমি ’রমজমা’ বা বর্গা নিয়ে চাষ করতে হয়। হাওরবাসি কৃষক এখন আর ঘরের বীজ ব্যবহার না করে কোম্পানির বীজের উপর নির্ভরশীল হয়ে পরেছে। অধিক দাম দিয়েই তাঁদের এ বীজ কিনতে হয়। হালচাষ, বীজতলা তৈরী, সার, সেচকর, কীটনাশক, আগাছা দমন, কর্তণ, পরিবহণ, মাড়াই-ঝাড়াই, শুকানো সব কিছুই তাঁদের টাকা/ ধানের বিনিময়ে সম্পন্ন করতে হয়। হাওরের সর্বত্র বিদ্যুত না থাকায় কৃষককে ডিজেল চালিত সেচ ব্যবস্থার উপর নির্ভর করতে হয়। এতে ধান উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়। খরচকৃত এ টাকা তাঁদের মহাজনের কাছ হতে লগ্নি/দাদন/ঋণের মাধ্যমে যোগার করতে হয়। দাদনের ব্যয়িত এ টাকার উপর মাত্র ৩-৬ মাসের জন্য শতকরা ৫০ টাকা হারে লাভ/সুদ দিতে হয়। ব্যাংক থেকে পর্যাপ্ত কৃষি ঋণ না পাওয়ায় তাঁরা মহাজনের কাছ হতে দাদন নিতে বাধ্য হয়। ব্যাংকগুলো কৃষকের ঋণ চাহিদার শতকরা ১০ ভাগও পূরণ করে না।
হাওরের প্রাণকেন্দ্র কিশোরগঞ্জের ইটনার বীর মুক্তিযোদ্ধা রওশন আলী রোশো ভাই এক একর জমি আবাদে খরচের যে হিসাব দিয়েছেন তা সুপ্রিয় পাঠকের অবগতির জন্য প্রদত্ত হলোঃ
১. জমির জমা (রমজমা/বর্গা)-১৬,০০০/-
২. বীজ (৫ কেজি, হাইব্রিড)- ১২,০০/-
৩. হালচাষ-১,৫০০/-
৪. বীজতলা তৈরী- ২০০/-
৫. চারা (জালা) উত্তলন- ৬০০/-
৬. চারা রোপন- ২,০০০/-
৭. সার-৪,০০০/-
৮. আগাছা পরিষ্কার করা- ৪০০/-
৯. কীটনাশক-৫০০/-
১০. ছয়মাসি কামলা (শ্রমিক)- ৩,০০০/-
১১. ধান শুকানো বাবদ খরচ- ৬০০/-
মোট টাকা = ৩০,০০০/- (তিরিশ হাজার টাকা মাত্র)
এছাড়াও উৎপাদন খরচের অংশ হিসাবে নগদ উৎপাদিত ধান প্রদাণ করতে হয় নিম্নোক্ত হারে ঃ-
১. সেচকর- ৩ মণ (বিদ্যুত/মটর); ৭ মণ (ডিজেল)
২. ধান পরিবহণে ট্রলি / নৌকা ভাড়া – ৩ মণ
৩. ধান কাটা (উৎপাদিত ধানের ১০%; ফলন ৬০মণ/একর )- ৬ মণ
৪. মাড়াই (মাড়াই ধানের ৫%; ফলন ৬০মণ/একর)- ৩ মণ
৫. ছয়মাসি কামলা (শ্রমিক)- ১০ মণ
মোট ঃ ২৫ মণ (বিদ্যুত); ২৯ মণ (ডিজেল) ধান (পচিশ বা উনত্রিশ মণ ধান)।
এ হিসাবে গিরস্থি করতে গিয়ে সাত পুত, তের নাতির শ্রমকে বিবেচনায় নেয়া হয়নি। আগাম বন্যা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে ধান কাটা, পরিবহণ ও মাড়াই এর খরচ বেড়ে যায় কয়েক গুণ। অনেক সময় তা আধাআধিতে দাঁড়ায়। উৎপাদন খরচ এবং উৎপাদন ফলাফলের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে দেখা যাক ঃ
এক একরে আয় = উৎপাদন ৬০ মণ @ ৫০০ টা./মণ (বর্তমান দর) = ৩০,০০০ টাকা।
এ ৬০ মণ ধান উৎপাদন করতে কৃষককে নগদ ৩০.০০০ টা. + ২৫ বা ২৯ মণ ধান ব্যয় করতে হচ্ছে। ২৫ বা ২৯ মণ ধানের মূল্য হচ্ছে ২৫@ ৫০০ টা.=১২,৫০০টা. বা ২৯@ ৫০০টা.=১৪,৫০০টাকা। মোট খরচ হচ্ছে (৩০,০০০টা.+১২,৫০০টা. বা ১৪,৫০০টা.)= ৪২,৫০০টা. বা ৪৪,৫০০টাকা। অর্থাৎ এক মণ ধান উৎপাদন করতে বিদ্যুত চালিত সেচ ব্যবস্থায় খরচ ৭০০ টা. এবং ডিজেল চালিত সেচ ব্যবস্থায় ৭৫০ টাকা।
নগদ খরচের ৩০,০০০/-টাকা যদি কৃষক লগ্নি/দাদন নিয়ে থাকেন, তবে তাঁকে লাভ/সুদ (৫০%) দিতে হবে ১৫,০০০/- টাকা যাতে উৎপাদন খরচ বেড়ে হবে ৯৬০/- টা. (বিদ্যুতে) এবং ডিজেলে ১,০০০টা./মণ। বর্তমানে হাওর এলাকায় মোটা ধান ৪০০-৪৫০/- টা. এবং ব্রিধান ২৮, ২৯ বিক্রি হচ্ছে ৫০০/ টাকা মণ দরে। উৎপাদন খরচ বেড়েছে অনেক, উল্টো ধানের দাম কমেছে মণ প্রতি ১০০-২০০ টাকা হারে।
এখন দেখা যাক হাওরবাসি কৃষকের ঘরে কত মণ ধান উঠে ? নগদ টা. ৩০,০০০/- খরচ করে কৃষক পাচ্ছে (৬০ মণ-২৫বা ২৯ মণ) = ৩৫ বা ৩১ মণ ধান মাত্র। এতে তাঁর ধান উৎপাদন খরচ হবে মণ প্রতি যথাক্রমে ৮৬০টা. বা ৯৭০টা.। এ দামে ধান বিক্রি করতে পারলেই শুধু কৃষকের উৎপাদন খরচ উঠে আসবে, কমে একর প্রতি ১২-১৫ হাজার বা তার চেয়েও বেশী টাকা ক্ষতি হবে। ব্যয়কৃত লগ্নির টাকার লাভ হিসাবে ধরলে এ খরচ হবে অবিশ্বাস্য ও আকাশচুম্বি।
কিছুটা অবস্থাপন্ন কৃষক এ অবস্থায় নিজস্ব জমি ও টাকা ব্যয় করে চাষ করে কোন মতে অস্থিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারলেও বর্গা বা প্রান্তিক চাষীদের অস্থিত্ব হবে চরম বিপদাপন্ন ও হুমকির সম্মুখিন। প্রান্তিক চাষী ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হবে। হাওর এলাকায় সস্তা, উর্বর অনেক জমি ও অন্যান্য সুবিধার কারনে অতীতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হতে হাজার হাজার মানুষ বসতি স্থাপন করে পতিত জমিকে আবাদি জমিতে পরিণত করেছে । বসতি স্থাপনের একশত বছরের মধ্যে হাওরে উল্টো বাতাস বইতে শুরু করেছে। হাওরবাসি মানুষ ফসল হারিয়ে, চাষে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ঘরে ’খিল দিয়ে’ শহরমূখী হয়ে ইটভাটা বা পাথর খোয়ারীতে কর্মসংস্থাপনের মাধ্যমে বেঁচে থাকার অবলম্বন খুজছে। বর্ষার সাত মাস ব্যাপী বেকার ও কর্মসংস্থানের অভাব হাওরবাসির অভিবাসন স্রেুাত আরোও বাড়িয়ে দিচ্ছে। বাংলাশে জাতীয় সংসদের মানণীয় স্পিকার আব্দুল হামিদের ভাষায় ” সারা দেশে লোক বাড়ে, কিন্তু হাওরে লোক সংখ্যা কমছে।” কাজের অভাবে অভিবাসনই এর মূল কারণ।
হাওরের কৃষককে সব সময়ই ফসলহানি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভয়ে একটা আতংক ও শংকার মধ্যে থাকতে হয়। এই বুঝি শুরু হলো ’আফাল’ এর ’তাফালিং’; আগাম, অকাল বন্যা। সারা বছরের অর্থ, রক্ত ঘাম ও শ্রমে আবাদকৃত জমির ধান কাটতে হয় মাত্র কয়েক দিনে। এক মুহূর্তের দেরী, নিমিষেই চোখের সামনে তলিয়ে যেতে পারে আধা পাকা, কাঁচা ধান। তখন বানের ঘোলাজল আর কৃষকের চোখের লুনাজলে সব কিছু সয়লাব হয়ে পরে। সে সময়ে কৃষকের দূরাবস্থা চোখে না দেখলে লিখে বুঝানো কষ্টকর। নাকানি চুবানিতে নাকের আর চোখের পানিতে সব একাকার হয়ে যায়। কাটার পরপরই অধিকাংশ ধান বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়। কারন, সংকীর্ণ বাড়ি/গ্রাম ওয়ারিশানদের মাঝে বণ্টন হতে হতে ছোট পরিসরে ঘুমানোরই জায়গা নেই, ধান রাখবে কোথায় ? তার উপর ঋণ, কর্জ হাসিল এবং সারা বছরের চাহিদার উপোষের প্রয়োজন মিটানোর ব্যাপার সেপার তো রয়েছেই। সিডর, আইলা’র চেয়েও ভয়াবহ নিরব ও স্থায়ী দুর্ভোগ পোহায় তাঁরা। ধান বিক্রিতে ওজনের কারসাজি ও ঠকানো ওপেন সিক্রেট। নতুন গ্রাম সৃজন এবং এর চারিপাশে বছর ব্যাপী মৎস্য চাষের জন্য পুকুর খনন, এ থেকে কিছুটা নিস্কৃতি দিতে পারে। শহরের ল্যান্ড ডেভেলাপারগণ বিষয়টি ভেবে দেখতে পারেন। এটি অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসা হবে। হাওর এলাকায় বলতে গেলে সরকারিভাবে ধান কিনা হয় না। নেই বড় কোন গোদাম ও রাইচ মিল বা চাতাল। ফলে সব ধান বড় বড় নৌকায় করে চলে যায় হাওর এলাকার বাহিরে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে, এ ধান ফিরে আসে মূল্য সংযোজিত হয়ে-চাল হয়ে, অধিক দামে। এতে দ্বিমুখী ক্ষতিতে কৃষকের দুর্ভোগ ও ভোগান্তির মাত্রা বেড়ে যায় অনেক গুণ। এক বছরের ফসলহানির জের তাঁদের বহন করতে হয় কয়েক বছর যাবৎ।
যুগ যুগ ধরে এ ধারা চলে আসলেও আমাদের কৃষকের সুরক্ষা নিয়ে তেমন একটা আলোচনা, আন্দোলন হয়নি। চাষী বা কৃষক সমাজ সব সময় উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য না পেয়ে, অবহেলিত বা অবজ্ঞার পাত্র হয়ে প্রতিবাদহীনভাবে, নিরবে-নিবৃত্তে খাদ্য উৎপাদন অব্যাহত রেখে চলেছে। কত দিন ? কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাও তো এক ধরণের ব্যবসা। ক্ষতি দিয়ে ব্যবসা চলে না। এ অবস্থায় বিকল্প কর্মসংস্থান পেলে অধিকাংশ হাওরবাসি কৃষক ধান উৎপাদনে জড়িত হতো না। বাজারে চালের মূল্য তো কম নয়। কিন্তু কৃষক এর সুফল পাচ্ছে না। কৃষকের কথা না ভেবে, অবিবেচকের মতো শহরবাসি সস্থায় খাবার চায় এবং সরকারও এ থেকে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করতে তৎপর। মধ্যস্বত্ব ভোগীদের দৌরাত্ব বেড়েই চলেছে, সব লাভ তাঁদের ঘরে উঠে। তাঁদের নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। একজন নেতা ’গুম’ হলে হরতাল হয়, লক্ষ্য কৃষক ধুকে ধুকে নিঃশেষের দিতে ধাবিত হলেও কোন রাজনৈতিক দল এ নিয়ে কথা বলছে না, হরতাল দিচ্ছে না, কেন ? এ আতœঘাতি নিরবতা আমাদের নিঃস্ব করে দেবে !
বর্তমান সরকার হাওরবাসি কৃষককে উৎপাদনে সর্বতোভাবে সহায়তা দিয়ে আসছেন। কিন্তু কৃষক বান্ধব এ সরকার ধান ক্রয়ে/দাম নির্ধারণে নিরব কেন ? হাওরবাসি সব সময়ই প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক ও মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষ শক্তিকে সমর্থন দিয়ে আসছেন। ফলস্রুতিতে, দীর্ঘ সময়ব্যাপী রাষ্ট ক্ষমতায় অধিষ্ট বিপক্ষ শক্তির কাছ থেকে হাওরবাসি কাঙ্খিত উন্নয়ন সহায়তা পায়নি। বর্তমানেও যদি তাঁদের ’কপাল পুড়ে’, তবে হাওরবাসি বিগড়ে যেতে পারে! হাওর নিয়ে খাদ্য মন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক এর আশা জাগানিয়া বক্তব্য আমাকে আশাবাদি করে, আমি স্বপ্ন দেখি। হাওরের সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে তিনি অনেক দিন গবেষণা করেছেন। ধানের ন্যায্য মূল্য হতে বঞ্চিত হলে তাঁরা হতাশ ও ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে উৎপাদনে নিরুৎসাহিত হবেন। খাদ্য নিরাপত্তার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন কৃষক সুরক্ষা । কৃষককে বঞ্চিত রেখে দীর্ঘ মেয়াদী উচ্চ উৎপাদন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা সম্ভব নয়। নিষ্টাবান কৃষি মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরীর দরদী হস্তক্ষেপ এ বঞ্চনা হতে মুক্তি দিতে পারে। শুধু ধান চাষ নির্ভরশীল না থেকে শস্য বহুমুখী উৎপাদন ও আধুনিক মৎস্য চাষ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। দেশের অর্থনীতি কৃষির উপর নির্ভর করে, ভোটের সংখ্যার দিক দিয়েও কৃষকের সংখ্যা অনেক বেশী। তবে কেন, কৃষককে তাঁর ফসলের ন্যায্য মূল্য না দিয়ে, শহরের মুষ্টিমেয় লোককে সস্তায় চাল খাওয়ানো ও সমালোচনার ভয়ে বঞ্চিত রাখা ? ভোটের হিসাবে এ টেকনিক কতটুকু কার্যকর হবে, আমি সন্দিহান ? আর তা হবে ’ বেঁচে থাকার জন্য মৃত্যুর দিকে ধাবিত হওয়া’র সমতুল্য।
ড. নয়িাজ পাশা, কৃষি প্রকৌশলৗ, হাওর ভূমপিুত্র । ফোনঃ- ০১৭২ ৭০৭৪ ৫৮৪ । niazpasha@yahoo.com
(২০১০ এ হাওরের অকাল বন্যার পর রচিত )
Address: Dr. Niaz Pasha, Senior Technical Officer, SAARC Agriculture Centre, BARC Campus, Farmgate, Dhaka (Ex VP. Fazlul Haque Hall Student union, BAU, Mymensingh)
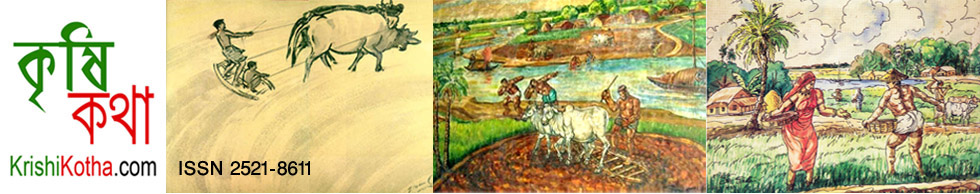
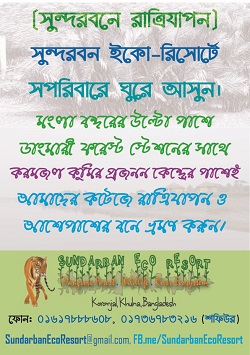




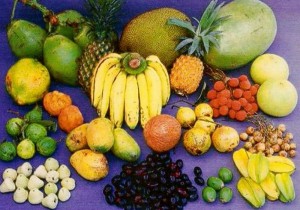







 Visit Today : 95
Visit Today : 95 Total Visit : 173150
Total Visit : 173150